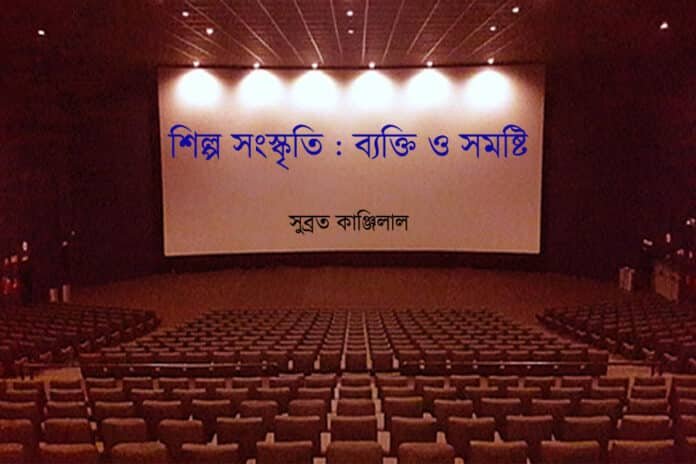সুব্রত কাঞ্জিলাল
উৎপল দত্তের দলের লোকেরা বলতেন, আমরা কলকাতার হলগুলোতে অভিনয় করে তৃপ্তি পাই না। কলকাতার বাইরে নাটক করতে গিয়ে যখন দেখি সামনে হাজার হাজার কালো কালো মাথা তখন আমাদের এনার্জি লেবেল বেড়ে যায়। অনেকেই হয়তো জানে না যে আমাদের দলের অভিনেতাদের অভিনয় শেখাবার সময় উৎপলদা এই ভাবেই ট্রেন্ড করতেন।
কলকাতা শহরের এলিট থিয়েটারের বাইরে একাঙ্ক নাটক নিয়ে শুরু হয়েছিল বিপুল চর্চা। এমন কোন গ্রাম, গঞ্জো, মহকুমা শহর, জেলা ছিল না যেখানে বাঁশ কাঠ দিয়ে মঞ্চ বেধে নাটকের উৎসব হতো না। সেইসব উৎসবেও লক্ষ লক্ষ মানুষ রাতের পর রাত জমায়েত হতেন বাংলার শত শত নাটকের দলের নাটক দেখতে। কোন কোন মঞ্চের বাইরে আমরা দেখতাম হাজার খানেক দর্শক বসে আছে। 5/-10000 দর্শকও অনেক মঞ্চে দেখা যেত। এইসব উৎসবগুলো ছিল বাংলার ১২ মাসের ১৩ পার্বণের মত। এখানেও যারা অভিনয় করতে আসতেন তাদের নাটকগুলো সর্বত্র গামী হয়ে উঠেছিল। একইভাবে এইসব মঞ্চের অভিনেতারাও জনতার দরবারে নাটক অভিনয় করার জন্য বিশেষভাবে ট্রেন্ড হতেন।
অন্যদিকে এমন অনেক রথী মহারথীদের (নাম উচ্চারণ করছি না) বলতে শোনা গেছে যে , আমাদের নাটকগুলো যে কোন মঞ্চে অভিনয় যোগ্য নয়। নাটক সেই ভাবেই বাধা হয়। শম্ভু বাবু বলতেন, আমাদের থিয়েটার আসলে মাইনরিটি কালচার। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলতেন, আমার কবিতা সর্বত্রগামী হয়ে উঠতে পারে নি। এটা আমার ত্রুটি। আমি সেই কবির জন্য কান পেতে আছি যে থাকবে মাটির কাছাকাছি।
ফরাসি দার্শনিক নাট্যকার রোমা রোলা পিপলস থিয়েটারের থিসিস লিখতে গিয়ে জনগণ অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের কথা ভেবেছিলেন। তার নির্দেশ ছিল এই রকম যে, সারাদিন শ্রমজীবী মানুষ হাড় ভাঙ্গা খাটুনির পরে যখন থিয়েটার দেখতে আসবে সেই থিয়েটারকে ওই মানুষগুলোর মনোরঞ্জন করতে হবে।
চল্লিশের দশকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ওই পথেই অগ্রসর হয়েছিল। ডাক্তারি চেম্বার খুলে রোগীর জন্য বসে থাকলে চলবে না। ডাক্তারকে যেতে হবে বস্তিবাসী গ্রামবাসী মানুষদের কাছে। চারণ কবিদের মতো, লালন ফকিরের মত বাউলদের পথে চলতে হবে জনগণের থিয়েটারকে।
পৃথিবীর দেশে দেশে জনগণের নাট্যচর্চা সভ্যতার ঊষা লগ্ন থেকে চলে আসছিল। আমাদের দেশেও বিভিন্ন রাজ্যে এই থিয়েটার ছিল। তবে হ্যাঁ থিয়েটার শব্দ টা প্রচলিত ছিল না। যাত্রা, ঝুমুর গান, গম্ভীরা, আলকাপ, তরজা গান বা কবিগান, পুতুল নাচ, আরো অনেক নামে যেসব লোকনাট্যের প্রচলন ছিল সেখানে চিরকাল সমষ্টি মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।
উত্তর ভারতে আরবি, ফারসি, উর্দু ভাষায় যেসব কাব্য রচনা হতো সেখানেও দেখা যাচ্ছে কবিরা জনসমক্ষে এসে কাব্য পাঠ করছেন। একইসঙ্গে শ্রোতাদের ও আহ্বান করা হতো কাব্য পাঠে অংশ নিতে। হিন্দি ভাষী অঞ্চলে রাম যাত্রার প্রচলন ও জনপ্রিয়তার কথা আমরা জানি। আমাদের বাংলাতেও আগেকার দিনে রাম যাত্রার আসর ছিল। বিপুল জনপ্রিয়তা ছিল।
পৃথিবীর সর্বত্র কায়িক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরা তাদের শ্রম লাঘব করার জন্য গান গাইত। আমাদের বাংলায় যেমন মাঝিমল্লাদের গান যাকে ভাটিয়ালি বলা হয়। ধান রোপন করার গান। ছাদ পেটানোর গানের সুর নিয়ে শচীন দেব বর্মনরা কালজযয়ী আধুনিক গান সৃষ্টি করে গেছেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবদান ও কম নয়। পালকি বেহারাদের নিয়ে সলিল চৌধুরী এবং ভূপেন হাজারিকার যুগান্তকারী সংগীত সৃষ্টি হয়েছিল।
অর্থাৎ এটা পরিষ্কার যে শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে ব্যক্তির ভূমিকা নগণ্য না হলেও সমষ্টির ভূমিকা কোনদিন অস্বীকার করা যায় না। একজন কবি যখন কাব্য রচনা করেন তখন তার পাঠক বা শ্রোতার প্রয়োজন হয়।। যুগে যুগে বাউল সাধকরা তাদের সংগীত গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে প্রচার করে গেছেন। তারা জানতেন যে গৃহ কোণে বসে একান্তে শিল্পচর্চার কোন অর্থ হয় না।
অন্যদিকে শুধুমাত্র বাণিজ্যের প্রয়োজন মেটানোর জন্য মানুষের শিল্প গড়ে ওঠে না। রাজতন্ত্রের যুগে সামন্ত প্রভুরা অনেকেই তাদের প্রাসাদে নানা স্তরের শিল্পীদের নিয়ে আসতেন। তানসেন থেকে শুরু করে কালিদাস হয়ে ভারতচন্দ্র এই ভাবেই তাদের শিল্প রচনা করে গেছেন। মুঘল যুগে শিল্পচর্চার গতিবেগ প্রবল হয়েছিল। স্থাপত্য শিল্প, বয়ন শিল্প, চিত্রশিল্প, সংগীত এবং নৃত্য কলা উর্দু এবং ফারসি কাব্য এই সময় চিরায়ত মূল্য প্রতিষ্ঠা পেয়ে ছিল।অবশ্য তারও আগে, বৌদ্ধ যুগের শিল্প নিদর্শনগুলো আমাদের ভারতের অন্যতম অহংকার। অজন্তা ইলোরা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অজন্তা ইলোরাতে শিল্প রসিকরা এসেছেন। বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।
যদিও সামবেদের যুগে যৌথ সংগীতের চর্চার কথা বলা আছে। নানারকম যাগ যজ্ঞে যেসব বেদগান রচনা করা হয়েছিল সেগুলোও আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্যের অংশ। বারবার মনে রাখতে হবে যে এই সব সংগীত কোন একক ব্যক্তির গান নয়। যৌথ সংগীত যাকে বলা হয় বৃন্দ গান। সম্ভবত এই ধারা থেকে আধুনিক যুগে কয়ার সংগীতের প্রচলন হয়েছিল। এইখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ধন- তন্ত্র, সংসদীয়গণতন্ত্র, পুঁজিবাদের বিকাশের মধ্য দিয়ে যৌথ শিল্পচর্চার বিরুদ্ধে আঘাত আসতে থাকে। ধণতন্ত্রের আওতায় যৌথ মানুষের প্রাসঙ্গিকতা লুপ্ত হতে থাকে। ধনতন্ত্র ব্যক্তি মানুষের প্রাসঙ্গিকতায় জোর দেয়। ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলে। প্রকৃতপক্ষে বাজারী পৃথিবীতে ব্যক্তিরও কোন ভূমিকা নেই। দোকানদারি সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিও আসলে পণ্য।
এই ব্যবস্থার মালিকরা প্রথম থেকেই সেই সব শিল্পের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে থাকে যে শিল্পের উপভোক্তা সাধারণ মানুষ। এরা যাত্রা থিয়েটার এর উপর নানারকম ছলচাতুরি করে বন্ধ করে দিতে চেয়েছে। থিয়েটার যে ছোটলোকদের ব্যাপার, পতিতা মাতাল, চোর জোচ্চোরদের আখড়া একইসঙ্গে গির্জার বিরোধী এইটা প্রচার করেছিল ইউরোপের দেশে দেশে। আমাদের দেশেও ব্রাহ্মণ্য সমাজ একইভাবে প্রচার করেছে যে গিরিশ ঘোষেরা চরিত্রহীন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক নম্বর চরিত্রহীন এবং মাতাল এই প্রচারটা শক্তিশালী ছিল। গান-বাজনা করে পতিতা বাঈজীরা। ওটাই তাদের পেশা। খরিদ্দার ধরবার উপায়। একইভাবে মৌলবীরা শরীয়তের নাম করে চার্চের পাদ্রী আর মন্দিরের পুরোহিতদের কন্ঠে কন্ঠ মিলিয়েছে।
আসলে যে শিল্প উপভোগ করবার জন্য হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয় পুজির মালিকদের আসল ভয় এইখানে। এই ধারায় দেখা যাচ্ছে সিনেমা শিল্পের সংকট প্রকট হয়ে উঠেছে। মালিকরা বলতে চায় ঘরে বসে টেলিভিশন দেখো। একা একা মুঠোফোনের পর্দায় সিনেমা দেখো। অর্থাৎ ব্যক্তিকে সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার অনন্ত প্রচেষ্টা।
স্বাধীনতা প্রাপ্তি র পরের ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক মহলের চিত্রটা কি রকম? সিনেমা শিল্পে প্রথম থেকেই এক ধরনের কড়া সেন্সরশিপ ছিল। এর আসল কারণ সরকার বিরোধী সমালোচনা মূলক বক্তব্য আটকানো। বেতার কেন্দ্র ছিল সরকারের প্রচার যন্ত্র। দৈনিক পত্র-পত্রিকাগুলোকে পর্যন্ত কড়া সেন্সারশীপের মধ্য দিয়ে যেতে হতো। বহুবার বহু নাটক থিয়েটার সরকারের পেয়াদা বন্ধ করে দিয়েছিল। নাট্যকার নাট্যকর্মীদের বারবার জেলে ঢোকানো হয়েছে। তবুও বলা যায় কংগ্রেসী সরকারগুলো সংবিধানের প্রতি যতটা যত্নশীল ছিলেন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থা প্রকাশ করতো সেই অবশেষ টুকুও একেবারে ঘুচিয়ে দিয়েছে পরবর্তী সরকার। থিয়েটার সিনেমা থেকে শুরু করে সব রকম সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি এরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আর্থিক মূল্যে শিল্পীদের কিনে নেবার নানা রকম কৌশল শুরু হয়েছে। থিয়েটার , সিনেমা , সঙ্গীত জগতের ও সাহিত্যকর্মীদের একাংশকে ক্রীতদাস বানিয়ে ফেলেছে। এসবের মধ্যে থেকে অতি সামান্য হাতে গোনা যেসব সংস্কৃতিক কর্মীরা কাজ করছেন তাদের কাজের মধ্যে শিথিলতা, নানা রকম দুর্বলতা, বৃহত্তর জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা দেখা যাচ্ছে।
এরা কলকাতার শীতাতপ মঞ্চে হাতে গোনা কিছু নির্দিষ্ট দর্শকের মধ্যে কাজ করছেন। বৃহত্তর জনগণের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। সেই কারণেই এইসব কাজও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারছে না। ্ অন্যদিকে তাদের এইসব কাজ কোনভাবেই সৃষ্টিশীল বলা যাবে না। পুরনো জনপ্রিয় নাটক নিয়ে যেমন রিমেকিং চলছে অন্যদিকে নাটক রচনা থেকে শুরু করে প্রয়োগ কৌশলে যান্ত্রিকতা এত বেশি যার চাপে হৃদয় বৃত্তি হারিয়ে যাচ্ছে। মননশীল অভিনয় যার মধ্যে বুদ্ধির ছাপ থাকবে সেটাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোন কোন পরিচালক নিজেকে ইন্টেলেকচুয়াল প্রমাণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। নাটকের অভিনয়ের দিনে দু তিনজন দর্শকের পিঠ চাপড়ানো মন্তব্য ফেসবুকে আপলোড করে আত্মপ্রচারের ব্যর্থ চেষ্টা চলছে। আজকাল প্রচারের ঢাক বাজাতে খুব বেশি পয়সা খরচা হয় না। ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ টুইটার কাজটা করে দেয়। এইসব নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে বর্তমান ভারতবর্ষের জীবন্ত সমস্যাগুলোর সম্পর্ক কোথায়? এই প্রশ্নটা তুলেছিলেন জনৈক প্রবীণ সাংবাদিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মী। তিনি আরো বলেছিলেন, আগে জনপ্রিয় নাটকগুলো যেভাবে কলশো পেতো আজকাল সেভাবে পায় না কেন? তার একটা অন্যতম কারণ আছে। সরকারের অনুদান নিয়ে যে নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে, সেই নাটক নিয়ে প্রযোজকদের মাথা ব্যাথার কারণ থাকে না। দর্শক সমালোচকদের তোয়াক্কা করবার কি দরকার? নাটকের গুণমান নিয়ে ভাববার সময় কোথায় ? টাকা যোগাচ্ছে গৌরী সেন।
নাসির উদ্দিন শাহ যখন বলেন, সিনেমার সেলিব্রেটি স্টারদের মঞ্চে দেখার জন্য দর্শকদের টিকিট কেনার প্রবণতা বেড়ে গেলে থিয়েটার অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। এই ব্যবস্থায় থিয়েটার ব্যবসা মালিকপক্ষকে মুনাফা দান করে। অনেকদিন আগে ইউরোপের একজন চলচ্চিত্র পরিচালক বলেছিলেন (লুই বুনুয়েল) সিনেমার সাদা পর্দা যদি সত্যি কথা বলতে পারতো তাহলে দেশে দেশে সমাজ বিপ্লব ঘটে যেত। আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি এটা ভেবে যে, ক্যামেরাকে বেশ করে আফিম খাইয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে।
বুনুয়েলের এই কথার তাৎপর্য আমরা এখন বুঝতে পারি—–শিল্প মধ্যম গুলোর প্রায় প্রতিটি মাধ্যমকে একইভাবে আফিম খাইয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। এই কারণেই ব্যক্তি মানুষের প্রাধান্য বাড়লেও সমষ্টি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের সব রকম পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।। ব্যক্তি মানুষগুলোও আত্মবিচ্ছিন্ন এক একটি দ্বীপের মত হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে বেড়ে চলেছে সামাজিক লুট, রাষ্ট্রীয় করাপশন, গণধর্ষণ, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন। এই প্রশ্নে শিল্পকর্মীদের ভূমিকা প্রশ্নচিহ্নের মধ্যে পড়ে গেছে। চার্লি চ্যাপলিনের মত বিদ্রোহী শিল্পীরা হারিয়ে যাচ্ছেন। গণতন্ত্রের স্বর্গরাজ্য
মার্কিন দেশে বসে তিনি যে সোজা মেরুদন্ডের ভূমিকা পালন করেছিলেন সেই ইতিহাস চাপা পড়ে যাচ্ছে। জনগণ এবং সমাজ বিচ্ছিন্নতা নিয়ে আর যাই হোক মহৎ শিল্প রচনা করা যায় না। প্রাত্যহিক জীবন সংগ্রামের গনগনে আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে জীবন শিল্পীরা রচনা করেন মানুষের শিল্প।